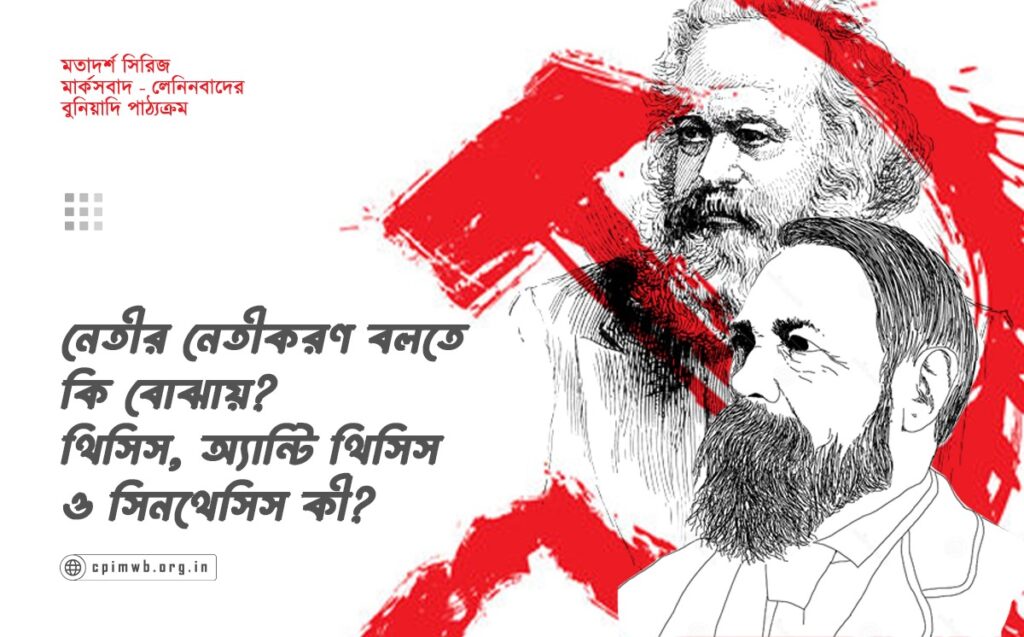প্রাককথন
অর্থনীতিবাদ অথবা যাকে আজকের দুনিয়ায় মধ্যবিত্ত সংস্কারবাদ (অথবা সুবিধাবাদ) বলা হয়, সেসবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল কার্ল মার্কসকে। ১৮৪৭ সালের ফ্রান্স, মার্কস তখন সে দেশের বাসিন্দা। পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁ প্রকাশ করলেন ‘দারিদ্র্যের দর্শন’, ইংরেজিতে ফিলোজফি অফ পভার্টি। বইয়ের পাতায় পাতায় বর্ণনা দিলেন রাষ্ট্রের মূলোচ্ছেদ প্রয়োজন বটেই, তবে তা হবে ব্যাক্তি মানুষের সততা, যোগ্যতা এবং নৈতিকতার উপরে ভর করেই, রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে কিছুই হবে না কেননা পচে গলে যাওয়া সমাজব্যবস্থা মানুষকে এতটাই দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলেছে যে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সংগ্রামে কোনকিছুই বদলাবে না।
এমন চমকপ্রদ বক্তব্যে প্রাচীন ঋষিদের বানীর ঝাঁঝ রয়েছে, অর্থনীতির নামে নৈরাজ্যের শাণিত উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সবচাইতে বেশি যা আছে তা হল সর্বহারার শ্রেণি রাজনীতিকে অকর্মণ্য করে দেওয়ার রাজনীতি! মধ্যবিত্ত শ্রেনি নিজের সামাজিক অবস্থানের কারনেই চিরকাল দোদুল্যমানতায় আক্রান্ত, শোষণমুক্তির প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিটোল, গোলাপ বিছানো পথেই সেই মুক্তি আসা চাই বলে নিজেদের নির্বাক বাসনাকে তত্ত্বের মোড়কে জাহির করে তারা। অর্থাৎ একদিকে বুর্জোয়াদের ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রতি মোহ আরেকদিকে নিপীড়িত, নির্বিত্ত মানুষের দুর্দশা দেখে ভয় ও বিদ্রোহের মেজাজে ভরপুর মধ্যপন্থী শ্রেনিচেতনা। সেই সময় ফ্রান্সে এহেন শ্রেণি বৈশিষ্টেরই সর্বোৎকৃষ্ট মেধা ছিলেন প্রুধোঁ। বুদ্ধিজীবীতার আড়ালে শাসকের পক্ষেই, স্থিতাবস্থার পক্ষেই অবস্থান নেওয়া সংশয়ী মনোভাবই যার, যাদের চেতনার মুল কথা।
লেনিন এদেরই দাঁড়ে বসা টিয়াপাখি বলে অভিহিত করেছিলেন।
প্রুধোঁর ‘দারিদ্র্যের দর্শন’র বিরুদ্ধে ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে ফরাসি ভাষায় ব্রাসেলস এবং প্যারিস থেকে প্রকাশিত হল মার্কসের লেখা ‘দর্শনের দারিদ্র’, পভার্টি অফ ফিলোজফি। দুরমুশ করে দেওয়া হল মেধার মধ্যবিত্তি। বিংশ শতাব্দিতে অরগ্যানিক ইন্টেলেকচ্যুয়ালস’দের ভূমিকা ব্যখ্যা করতে গিয়ে আন্তোনিও গ্রামশি যা কিছু লিখেছেন বলা যায় তারই সুত্রপাত ঘটেছিল মার্কসের লেখায়।
মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত (১৯৭৮) সংস্করণে উল্লিখিত রয়েছে – “পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পণ্য এবং অর্থ পরিচালনার চক্রাকার পদ্ধতি ব্যখ্যা করতে গিয়ে প্রুধোঁ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন, আগের বিষয় পরে ঠেলেছেন। যদিও বিনিময় মূল্যকে বুঝতে গেলে আমাদের বিনিময় ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তার ভুল হয়নি। বিনিময় পদ্ধতি বুঝতে প্রয়োজন হবে শ্রম বিভাজনকে বোঝার। আবার তাকে বুঝতে গেলে সমাজে শ্রম বিভাজনের দরকার হল কেন, এটাই সবার আগে উপলব্ধি করতে হয়। এই যে প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা, ঠিক এখানেই প্রুধোঁর ভ্রান্তি। শ্রমবিভাজনের প্রাথমিক শর্তটি বুঝতে যুক্তিগ্রাহ্য অনুমানই হল একমাত্র পথ। অথচ প্রুধোঁর কথামত কোনকিছু, এমনকি ইশ্বর সম্পর্কেও যদি অনুমান করতে হয় তবে তা হবে ভয়ানক অপরাধ, এমন করলে ঈশ্বরকে অস্বীকারই করা হবে। তাহলে নিজের বইতে প্রুধোঁ বিনিময় মূল্যকে আগাগোড়া অজ্ঞাত বিষয়রূপে চিহ্নিত করেও শ্রম বিভাজনকে কোন বিবেচনায় জ্ঞাত বিষয় হিসাবে অনুমান করে নিলেন?”
কথার জাল বিছিয়ে যারা মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে চায়, প্রকৃত প্রজ্ঞার মুখোমুখি হলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে তাকে বুঝতে উপরের ছোট্ট অনুচ্ছেদটুকুই যথেষ্ট। সেই বইয়ের একটি অংশই মতাদর্শ সিরিজের তৃতীয় প্রসঙ্গ- নেতির নেতিকরণ। একদিকে হেগেলের দর্শন ও আরেকদিকে অর্থনীতি প্রসঙ্গে প্রুধোঁ’দের মতামত- দুটিই এর প্রসঙ্গ। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিন্থেসিস সম্পর্কে মার্কসবাদী তত্ত্বের বুনিয়াদী দার্শনিক বোঝাপড়াকে উপলব্ধির কাজে কার্যকরী পাঠ।
কার্ল মার্কস
বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করেই সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এহেন যাবতীয় উৎপাদন সম্পর্ককে একজায়গায় এনে বিচার করলে সেটাই হয়ে ওঠে সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। এই যে সামাজিক কাঠামোকে উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে উপলব্ধি করা, একাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরগুলিকে চিহ্নিত করতে হয়। ঐ যে স্তরবিন্যাস তা আসলে সামাজিক কাঠামোর তাত্ত্বিক উপলব্ধি। বিদ্যমান বাস্তব পরিস্থিতির বিমূর্ত সারসংক্ষেপ। উদাহরণ হিসাবে বস্ত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া যায়। সুতী হোক বা সিল্ক, কাপড় তৈরির প্রক্রিয়ায় যুক্ত সকল মানুষের মধ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ঐ সম্পর্কসমুহ টেকে কতদিন? যতদিন অবধি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি একই থাকে। নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের রোজগারের ধরণ বদলাতে শুরু করে এবং সেই সুবাদে নির্মিত হতে শুরু করে নতুন ধরণের উৎপাদন সম্পর্ক। যতদিন হাপর বা হাতে টানা কলই (হ্যান্ডমিল) ছিল প্রধান ততদিন সমাজব্যবস্থার মাথায় ছিল সামন্ত প্রভুরা। যবে থেকে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এসে গেল তখনই আমরা শিল্প-কারখানার মালিক হিসাবে বুর্জোয়াদের (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিস্ট) দেখতে পেলাম।
উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্য বজায় রেখে মানুষ যে কেবল নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক নির্মাণ করে তাই না, সময়োপযোগী সমাজনীতিও একই সাথে গড়ে তোলে তারাই। সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে সক্রিয় প্রক্রিয়ার বদল ঘটার সাথেই সামনে চলে আসে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক সম্পর্কের নতুন স্তরসমূহ এবং সেইসব কিছুর সাথে তাল মিলিয়েই মানুষ নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, নিজেদের জীবনযাপনের ধারায় জরুরী সাদৃশ্য নির্মাণ করে।
সংশ্লিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের চেহারাটি যতক্ষণ অটুট রয়েছে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় সক্রিয় চিন্তা-ভাবনা, অর্থনৈতিক বিন্যাসসমূহের আয়ুষ্কালও কার্যত ততদিনই। বিদ্যমান সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনাগুলি কখনোই চিরায়ত হয় না। এদের বিবেচনা করতে হয় ইতিহাস নির্দিষ্ট পর্যায় ও ক্ষণস্থায়ী সত্য হিসাবেই।
সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বদাই নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশের পথে এগোতে থাকে। প্রগতির এহেন চলনের অভিঘাতেই নির্মিত হতে থাকে নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা, ভেঙ্গে পড়তে থাকে পুরাতন যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক। এই নিরন্তর প্রক্রিয়ায় যাবতীয় নশ্বরের ভিড়ে চিরস্থায়ী বলে যদি কিছু থাকে তবে তা হল গতিময়তার বিমূর্ত উপলব্ধিটুকু (নিজের লেখার এই অংশে ল্যুক্রেশিয়াসের রচনা অন দ্য নেচার অফ থিংস থেকে মার্কস একটি শব্দ উদ্ধৃত করেছেন- ‘মর্স ইমমর্টালিস’- আমরা তাকেই ‘চিরস্থায়ী নশ্বর’ বলেছি)।
অর্থনীতিবিদেরা ঠিক কি করেন? আমরা যাকে সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করেছি তারই কোনও এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যথাযথরূপে উপস্থাপন করাই অর্থনীতিবিদদের কর্তব্য। কিন্তু যখনই জানতে চাওয়া হয় কিভাবে ঐ সকল সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটল তখনই অর্থনীতি বেত্তাদের সীমাবদ্ধতা ফুটে ওঠে। সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ককে ইতিহাস নির্দিষ্ট সঞ্চারপথের সাথে মিলিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করাই উদ্ভবের কারনগুলিকে খুঁজে বের করার উপায়। কিন্তু অর্থনীতিশাস্ত্রীরা সেদিকে মনোযোগ দেন না… তাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু জীবনযাপনের বর্তমান উদ্দীপনাময় পরিসরেই ঘরাফেরা করে, তাই বর্তমান পরিস্থিতির শিকড় অন্বেষণে ব্যস্ত হলেই আমাদের সামনে যা পড়ে থাকে সেসবই হল ক্রমবিকাশমান উৎপাদন সম্পর্কের বিমূর্ত উপলব্ধি। উৎপাদন সম্পর্কের উৎস খুঁজতে আজকের অবস্থাকে যাবতীয় স্বতস্ফুর্ত ও সংগঠিত চিন্তাভাবনার ফলাফল হিসাবে দেখতে গেলেই আমাদের একটি কাজে বাধ্য হতে হয়। সেই কাজ হল মূর্ত বাস্তব থেকে বিমূর্ত উপলব্ধি হিসাবে এক চিরায়ত সত্যকে বিবেচনা করা। হেগেলের দর্শনশাস্ত্রে তাকেই ‘বিশুদ্ধ কারণ’ বা ‘হেতু’ বলা হয়েছে। ইতিহাসের গতিপথের একেকটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক চিন্তা-ভাবনাকে সামনে টেনে আনতে সেই ‘হেতু’ কিভাবে কার্যকরী হয়? একাজ সম্পন্ন করত সেই ‘বিশুদ্ধ কারন’টির সঞ্চারপথই বা ঠিক কেমন? তাহলে ঐ যে চিরায়ত হেতু তার পিছনের হেতুটি কোথায় গেল? এই অবধি এসে হেগেলের দার্শনিক প্রবচন প্রসঙ্গে যদি কেউ মহাশয় প্রুধো’র মতো সাহস দেখাতে পারেন তাহলে তিনি বলবেনঃ ঐ হেতু নিজেই নিজের থেকে আলাদা হিসাবে বিদ্যমান অর্থাৎ ওটি নিজেই নিজের কারণ ও ফলাফল দুইই। এরকম কথাবার্তার অর্থ কি?
‘চিরায়ত হেতু’ কিংবা ‘বিশুদ্ধ কারণ’ যে নামেই ডাকা হোক না কেন, অমন সত্য যদি নৈর্ব্যক্তিক হয় (অর্থাৎ নিজেই নিজের থেকে আলাদা বা ভিন্ন স্বত্বা হিসাবে টিকে থাকে) তবে তো তাকে আর নিজেরই ভরসায় সত্যরূপ হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। যে ‘বিশুদ্ধ কারণ’ নিজেই নিজের থেকে আলাদা সে না তো পারে নিজেকে ব্যখ্যা করতে (পজিশন), না পারে অন্য কারোর বিরুদ্ধ সত্ত্বা (অপোজিশন) হতে। নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলতেও (কমপোজিশন) তা অসমর্থ। এখানেই ঐ দার্শনিক উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা, সামাজিক সম্পর্কের গতিশীল বিকাশধারাকে চিরায়ত হিসাবে চিহ্নিত করার পরেও তার উৎসের ব্যখ্যা দিতে গিয়ে ঐ দর্শন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে একটা আস্ত মানুষ খাড়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই কাঠামোটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথার উপর ভর করে- অর্থাৎ উল্টানো অবস্থায়। কেতাবি ভাষায় নিজস্ব সত্তাটি (পজিশন) হল থিসিস, অপরের বিরুদ্ধসত্ত্বা হিসাবে কার্যকরী হওয়া (অপোজিশন) হল অ্যান্টিথিসিস এবং সবশেষে কোনও কিছুর স্বরূপ নির্ধারণে সমর্থ হওয়াকে (কমপোজিশন) বলে সিন্থেসিস। অর্থাৎ প্রথমে প্রমান (অ্যাফার্মেশন), তারপরে বিরুদ্ধপ্রমান বা অন্য প্রমানের নেতিরকরন (নেগেশন) এবং সবশেষে আগের নেতিকরনের পুনর্বার নেতিকরন (নেগেশন অফ দ্য নেগেশন)। এই হল ‘বিশুদ্ধ কারণ’র চলার ভাষা, যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ।
পরিবর্তনশীল জগতকে ব্যখ্যা করতে গিয়ে কোনও এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতকেই প্রকৃত কারণ হিসাবে তুলে ধরার পরিবর্তে আমরা এভাবেই বিশুদ্ধ সত্যের সঞ্চারপথটিকে তুলে ধরি। ব্যক্তিনিরপেক্ষরূপে সত্যের চেহারাটিকে উপলব্ধি করতে হলেও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।
বাস্তব পরিস্থিতি থেকে সত্যকে টেনে আনতে বিমূর্তকরণের যে প্রক্রিয়া তাতে যেভাবে সবকিছুই শেষ অবধি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টযুক্ত একেকটি বর্গের অধীনস্থ বিষয়ে পরিণত হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার খুব একটা কিছু আছে কি? এই প্রক্রিয়া কখনোই কোনও বিশ্লেষণাত্মক (অ্যানালিসিস) কাজ না, এ হল বস্তুগত সত্যের যুক্তিনিষ্ঠ সারসংক্ষেপ (অ্যাবস্ট্র্যাকশন)। উদাহরণ হিসাবে একটি বাড়ির কাঠামোর কথা ধরা যাক। যা কিছু দিয়ে ঐ গৃহের কাঠামোটি নির্মিত হয়েছে তাদের একেক করে বাদ দিতে দিতে এগোলে সবশেষে কি পড়ে থাকবে? একটি কাঠামোর ধারণা- যা আসলে কিছু নির্দিষ্ট পরিমান ‘স্থান’। এবার যদি স্থান’র মাত্রাসমূহকেও বিদায় জানানো হয় তবে আর কি থাকে? থাকে সেই বিশুদ্ধ পরিমান যা আসলে একটি যুক্তিনিষ্ঠ ধারণার নির্দিষ্ট বর্গ, আর কিছুই না। এই যে ধারণা সেটিই কি গৃহের অস্তিত্বের শিকড় হিসাবে কার্যকরী সেই বিশুদ্ধ কারণ’ নয়? এভাবেই চারপাশের বস্তুজগতের যাবতীয় কিছু সে সজীব হোক বা জড় পদার্থ তাদের সবকিছুকেই নিরন্তর বিমূর্তকরণের প্রক্রিয়ায় বিবেচনা করা যায় এবং তেমটা করলে শেষ অবধি ধারণার একেকটি যৌক্তিক বর্গ ব্যতীত আর কিছুই পড়ে থাকে না।
দুনিয়ার কার্য-কারণ ব্যখ্যা করতে গিয়ে অধিবিদ্যাবেত্তারা আসলে এটাই করেন। তারা যেভাবে এগোন তা হল বিমূর্তকরণ (অ্যাবস্ট্র্যাকশন) অথচ ভেবে বসেন তারা নাকি বিশ্লেষণ (অ্যানালিসিস) করছেন। এই প্রক্রিয়ায় এগোতে গিয়ে তারা প্রতিনিয়ত যত বেশি করে নিজেদের জগত বিচ্ছিন্ন করে তোলেন, তত বেশি করে কল্পনা করেন যে তারা ক্রমাগত এক বিশুদ্ধ সত্যের কাছাকছি পৌঁছতে পারছেন যা জগতের একেবারে মূল (কোর)-কে ভেদ করতে পারবে। যেকোনো সত্ত্বার মূল কারণ অন্বেষণে এহেন বিমুর্তকরণের প্রক্রিয়ায় যে বৃহত্তর সত্যের চিত্রপটটি ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে এটুকু তারা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেন। আর সেই সুবাদেই তারা ধরে নেন জগতসংসারের যাবতীয় কিছুই ঐ বিমূর্তকরণের মাধ্যমে যৌক্তিক বর্গীকরণের আওতাধিন হবে।
হেগেল ঠিক এভাবেই এগিয়েছিলেন। সেই জন্যই হেগেলীয় দর্শনে ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল জগতকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করতে ক্রমান্বয়ী ধারণার পরম্পরামাত্র। একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে মানুষের যাবতীয় কৃতকর্ম হিসাবে ইতিহাসের যে সংজ্ঞা তাকে তিনি ঐ যুক্তিতেই খারিজ করে দেন। ক্রমান্বয়ী ধারণার পরম্পরাকে নির্ভর করে জগতকে নতুন ও কার্যকারণ সম্মতরূপে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যস্ত থাকার সময় তিনি যা খেয়াল করেননি তা হল এই যে দুনিয়া বদলে যাওয়ার কারণ হিসাবে বিভিন্ন ধারণার প্রভাবকেই প্রধান মনে করার অভ্যাসটি কার্যত সকলের চেতনাতেই থাকে।
সামাজিক জীবনে আমরা যাকে প্রতিযোগিতা বলি তার উদ্ভব হয়েছিল একচেটিয়া সামন্ত শাসনের যুগে। একচেটিয়াপনার নেতিকরণ করতেই প্রতিযোগিতার সুত্রপাত, একচেটিয়া শাসনের বিরুদ্ধতাই (অপোজিশন) হল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার আবহকে নষ্ট করতে একচেটিয়া শাসনের উদ্ভব হয়নি। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যখন নতুন করে একচেটিয়া শাসনের কথাবার্তা সামনে আসছে তখন বুঝতে হবে তা সেই আগেকার একচেটিয়া ব্যবস্থা নয়। তাই আজকের যুগে একচেটিয়া বললেই তাকে যা নেহাতই বাস্তব পরিস্থিতির বিরুদ্ধ (অ্যান্টিথিসিস) মাত্র বুঝলে চলে না, আজকের দিনে (বুর্জোয়া ব্যবস্থায়) একচেটিয়া শাসন হল ইতিপূর্বের সংশ্লেষ (সিন্থেসিস)।
তাহলে বিষয়টি দাঁড়াল এরকম-
প্রমাণ (থিসিস) – সামন্ত যুগের একচেটিয়া শাসন, প্রতিযোগিতার আগেকার অবস্থা।
বিরুদ্ধ প্রমাণ (অ্যান্টিথিসিস) – প্রতিযোগিতা।
সংশ্লেষ (সিন্থেসিস) – আজকের একচেটিয়া শাসনব্যবস্থা। এ হল একইসাথে সামন্তবাদী একচেটিয়া শাসনের নেতি, কারণ এতে প্রতিযোগিতার বিষয়টি রয়েছে আবার আগেকার প্রতিযোগিতারও নেতি কারণ এই ব্যবস্থায় নতুন চেহারায় একচেটিয়া শাসনই গড়ে উঠছে।
তাই বুর্জোয়াদের একচেটিয়া শাসন কার্যত এক সংশ্লেষিত বন্দোবস্ত, এ এক এমন ব্যবস্থা যাকে নেতির নেতিকরন হিসাবেই বিবেচনা করতে হয় কারণ এতে দুই বিপরীত ব্যবস্থার ঐক্য হিসাবে উপলব্ধি করা যায়। এহেন একচেটিয়া শাসনই বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বাস্তব জীবনে আমরা যেমন প্রতিযোগিতা দেখতে পাই, তেমনই দেখা যায় একচেটিয়া অধিকার। এদের মাঝে স্বার্থের সংঘাত যেমন সত্য তেমনই সত্য এদুয়ের সংশ্লেষ। কিন্তু এহেন সংশ্লেষকে নিছক কোনও সুত্র (ফর্ম্যুলা) ভাবলে চলবে না। এদের সহাবস্থান স্থিতিশীল না, এ হল গতিশীল ঐক্য। একচেটিয়া অধিকার প্রতিযোগিতাকে প্রসারিত করে, আবার প্রতিযোগিতাও একচেটিয়া অধিকারকে এগিয়ে দেয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই একচেটিয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একসময় যারা ছিল প্রতিযোগী তাদেরই কেউ আজকের দিনে একচেটিয়া মালিক। এইবার যদি একচেটিয়া মালিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করতে চায়, নিজেদের মধ্যে আংশিক হলেও কিছুটা সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলে তখনকার অবস্থাটা কেমন হবে? তখন শ্রমিক-মজদুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে, ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ভবিষ্যতে যত বেশি মানুষ সর্বহারা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে ঐ প্রতিযোগিতা বাড়বে তত বেশি। তখন সর্বহারা শ্রেণি কেবল নিজের নিজের দেশের একচেটিয়া বুর্জোয়া মালিকদের সাথেই সংঘাতে জড়াবে না, সারা দুনিয়ার একচেটিয়া শাসনের সাথেও তাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে একচেটিয়া শাসন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে যদি তা ক্রমাগত নিজেকে বিবিধ প্রতিযোগিতাইয় লিপ্ত রাখতে পারে। অর্থাৎ একচেটিয়া শাসন যদি একটি সক্রিয় ও কার্যকরী সত্ত্বা (থিসিস) হয় তবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্যই প্রতিযোগিতার মতো বিরুদ্ধবাদের (অ্যান্টিথিসিস) সাথে তাকে সংশ্লেষিত (সিন্থেটিক) হতেই হবে।
প্রাককথন ও অনুবাদঃ সৌভিক ঘোষ